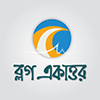শতবর্ষী কবি ফররুখ আহমেদ

এখন থেকে ১০০ বছর পূর্বে এই পৃথিবী আলো করে এসেছিলেন কবি ফররুখ আহমেদ। তিনি এমন একজন মৌলিক কবি ছিলেন, যিনি তাঁর সময়ের অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে পূণর্জাগরণের তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে তাদের অনুপ্রাণিতও করেছিলেন। এ জন্যেই তিনি বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁর কবি হিসেবে পরিচিতিও লাভ করেছিলেন।
অথচ এই ফররুখ আহমেদই ছাত্রজীবনে বামধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে চল্লিশ-এর দশকে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিবর্তন আসে এবং ইসলামী আদর্শকেই একমাত্র জীবন দর্শন হিসেবে পছন্দ করেছিলেন। হয়তো সেই চিন্তার আলোকেই তিনি ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। তাই বলে তিনি কখনও তাঁর বাঙালী সত্ত্বাকে বিসর্জন দেন নাই, তাইতো তিনি প্রয়োজনীয় সময় ঠিকই রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছিলেন।
শুধু তাই নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই কবি ফররুখ আহমদ আশ্বিন ১৩৫৪ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৭) সংখ্যা মাসিক সওগাত-এ, পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য নিবন্ধে লেখেন: গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
এ ছাড়াও ১৯৭১ সালে কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
কবি ফররুখ আহমেদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন পবিত্র রমজান মাসে মাগুড়া (তৎকালীন যশোর) জেলার শ্রীপুর উপজেলার মাঝআইল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং বাবা-মা তাঁর নাম রেখেছিলেন সৈয়দ ফররুখ আহমদ। কিন্তু কবি পরে সৈয়দ শব্দটি বাদ দেন। রমজান মাসে জন্মেছিলেন বলে দাদি তাঁকে রমজান বলেই ডাকতেন।
পিতা ছিলেন পুলিশ-অফিসার খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী এবং মাতা ছিলেন রওশন আখতার। ১৯৩৬ সালে খুলনা জেলা স্কুলের শিক্ষক কবি আবুল হাশেমের সম্পাদনায় স্কুল ম্যাগাজিনে কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।
১৯৩৭ সালে তিনি খুলনা জিলা স্কুল মতান্তরে কলকাতা মডেল এম.ই. স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আই.এ. পাস করেন। এরপর কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন নিয়ে বি.এ. অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯৪০ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে কলকাতা সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

তিনি তাঁর স্কুল ও কলেজ জীবনে যে সকল গুণী শিক্ষকদের সাহচর্য পান তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কথা-সাহিত্যিক আবুল ফজল, কবি আবুল হাশিম, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশ্দ, কবি আবুল হোসেন, কবি সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের সঙ্গে, সেই সাথে বন্ধু হিসেবে পেলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ লোহানীকে। এ সময়ই বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবির গুচ্ছ-কবিতা।
১৯৪১ সালে কবি তাঁর মুরশিদ, বিশিষ্ট আলেম অধ্যাপক আব্দুল খালেক সাহেবের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। তখন থেকেই বাম ধারার মতাদর্শ থেকে ক্রমান্বয়ে তিনি ইসলামী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। ফলে সে সময় লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কবির মাঝে মতাদর্শগত পরিবর্তন দেখা দেয় । তখন থেকেই তাঁর রচনায় ধর্মীয় ভাবধারার প্রভাব দৃশ্যমান হতে থাকে ।
কর্ম জীবনে প্রবেশের আগেই ১৯৪২ সালে তিনি তাঁর খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের (লিলি) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ে উপলক্ষেই কবি উপহার শীর্ষক একটি কবিতা লিখেন, যেটি ১৩৪৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে কবি ৮টি পুত্র সন্তান এবং ৩টি কন্যা সন্তানের জনক হন। তাঁরা হলেন - সৈয়দা শামারুখ বানু, সৈয়দা লালারুখ বানু, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাহমুদ, সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাসুদ, সৈয়দ মনজুরে এলাহি, সৈয়দা ইয়াসমিন বানু, সৈয়দ মুহম্মদ আখতারুজ্জামান [আহমদ আখতার], সৈয়দ মুহম্মদ ওয়হিদুজ্জামান, সৈয়দ মুখলিসুর রহমান, সৈয়দ খলিলুর রহমান ও সৈয়দ মুহম্মদ আবদুহু।
১৯৪৩ সালে কলকাতা আই.জি. প্রিজন অফিসে চাকরির মাধ্যমে কবির কর্ম জীবন শুরু হলেও দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বেতারে যোগ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কোথাও স্থায়ী ভাবে কর্মব্যস্ত থাকেন নাই। যেমন: ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইতে এবং ১৯৪৬ সালে জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে চাকরি করেন। এরই মাঝে তিনি ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী-র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের ১০ তারিখে কবির পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ইন্তেকাল করেন।
কবি ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় এসে ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে বহাল হন। বেতারের প্রয়োজনে কবি এখান থেকে নিয়মিত গান রচনা শুরু করেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্দ-নাত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনক্শা এসবও রচনা করেন।
পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কিশোর মজলিশ পরিচালনা শুরু করেন। তবে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিকের শাহাদতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা বেতারেই প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, যেখানে কবি ফররুখও সোচ্চার ছিলেন। ফলে কবি ফররুখ আহমদ সহ পনেরো জন শিল্পী ছাঁটাই হন। তার প্রতিবাদে বেতার শিল্পীদের সতেরো দিনব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফররুখ আহমেদ সহ সবাই চাকরিতে পুনর্বহাল হন এবং কবি টানা ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চাকরিতে বহাল থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই চাকরির ক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।
এ ঘটনার প্রতিবাদে আহমদ ছফা ১৯৭৩ সালে গণকন্ঠের ১৬ জুন সংখ্যায় একটি বিক্ষুব্ধ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং এ প্রতিবাদী প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কবি চাকরিতে পুনর্বহাল হন।
প্রতিবেদনে তিনি লিখেন, খবর পেয়েছি বিনা চিকিত্সায় কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে মারা গেছে। এই প্রতিভাধর কবি যাঁর দানে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে - পয়সার অভাবে তাঁর মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেননি, ওষুধ কিনতে পারেননি। কবি এখন বেকার। তাঁর মৃত মেয়ের জামাই, যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন বলে খবর পেয়েছি তাঁরও চাকুরি নেই। মেয়ে তো মারাই গেছে। যারা বেঁচে আছেন, কি অভাবে, কোন অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিনগুলো অতিবাহিত করছেন, সে খবর আমরা কেউ রাখিনি। হয়ত একদিন সংবাদ পাব কবি মারা গেছেন, অথবা আত্মহত্যা করেছেন।

দার্শনিক আহমদ ছফা
এরপর আরও লিখেন, ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে দু’টি উল্লেখযোগ্য নালিশ রয়েছে, সেগুলো হল - তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চল্লিশজন স্বাক্ষরকারীর একজন। তিনি স্বশ্রদ্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বাক্ষরদানকারী চল্লিশজনের অনেকেই তো এখনো বাংলাদেশ সরকারের বড় বড় পদগুলো অলংকৃত করে রয়েছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদকে একা কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে? পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না কে?।
এমন কি তাঁর প্রতিবেদনে তিনি কবি সুফিয়া কামাল এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক এ বি এম মুসা সহ অনেকেরই পাকিস্তান প্রীতির কথা তুলে ধরেছেন।
এত কিছুর পরও কবি ফররুখ আহমেদ বিরূপ পরিবেশের মধ্যে অনাদরে, অবহেলায় ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর, শনিবার, সন্ধ্যাবেলা (রমজান মাস) ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। শাহজাহানপুরে কবি বেনজীর আহমদের বাসস্থান ও মসজিদ সংলগ্ন আমবাগানে মরহুমের লাশ দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে বেনজীর আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর লাশও কবি ফররুখের পাশেই দাফন করা হয়।
কবি ফররুখ আহমেদ সাহিত্যের সব শাখায় বিচরণ করলেও তিনি কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর অসংখ্য লেখনীর মধ্যে নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থগুলো সর্বাধিক প্রশংসিত।
কাব্যগ্রন্থ:
সাত সাগরের মাঝি (ডিসেম্বর, ১৯৪৪)
সিরাজাম মুনীরা (সেপ্টেম্বর, ১৯৫২)
নৌফেল ও হাতেম (জুন, ১৯৬১)
মুহূর্তের কবিতা (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩)
ধোলাই কাব্য (জানুয়ারি, ১৯৬৩)
হাতেম তায়ী (মে, ১৯৬৬)
নতুন লেখা (১৯৬৯)
কাফেলা (অগাস্ট, ১৯৮০)
হাবিদা মরুর কাহিনী (সেপ্টেম্বর, ১৯৮১)
সিন্দাবাদ (অক্টোবর, ১৯৮৩)
দিলরুবা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪)
শিশুতোষ গ্রন্থ:
পাখির বাসা (১৯৬৫)
হরফের ছড়া (১৯৭০)
চাঁদের আসর (১৯৭০)
ছড়ার আসর (১৯৭০)
ফুলের জলসা (ডিসেম্বর, ১৯৮৫)
তাঁর প্রাপ্ত সম্মাননার বিবরণ নিম্নে দেয়া হ’লো:
১৯৬০ সালে একাডেমী পুরস্কার
১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদক প্রাইড অব পারফরমেন্স
১৯৬৬ সালে পান আদমজী পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার।
মরণোত্তর পুরস্কার:
১৯৭৭ সালে একুশে পদক।
১৯৭৮ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার।
১৯৭৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।
১৯৮০ সালের জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ফররুখ আহমদ রচনাবলি, ১ম খণ্ড প্রকাশিত।
১৯৮১ সালের জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ফররুখ আহমদ রচনাবলি, ২য় খণ্ড প্রকাশিত।
১৯৮২ সালে ঢাকায় ফররুখ একাডেমী প্রতিষ্ঠিত। প্রাতিষ্ঠানিক ফররুখ চর্চার শুরু।
১৯৮৩ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন কমিটি কর্তৃক অন্য নয়জন বিশিষ্ট ভাষা-সৈনিকের সাথে ভাষা-সৈনিক সংবর্ধনা ও পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান।
ট্যাগ ও ট্রেন্ডঃ
কোন মন্তব্য নাই.